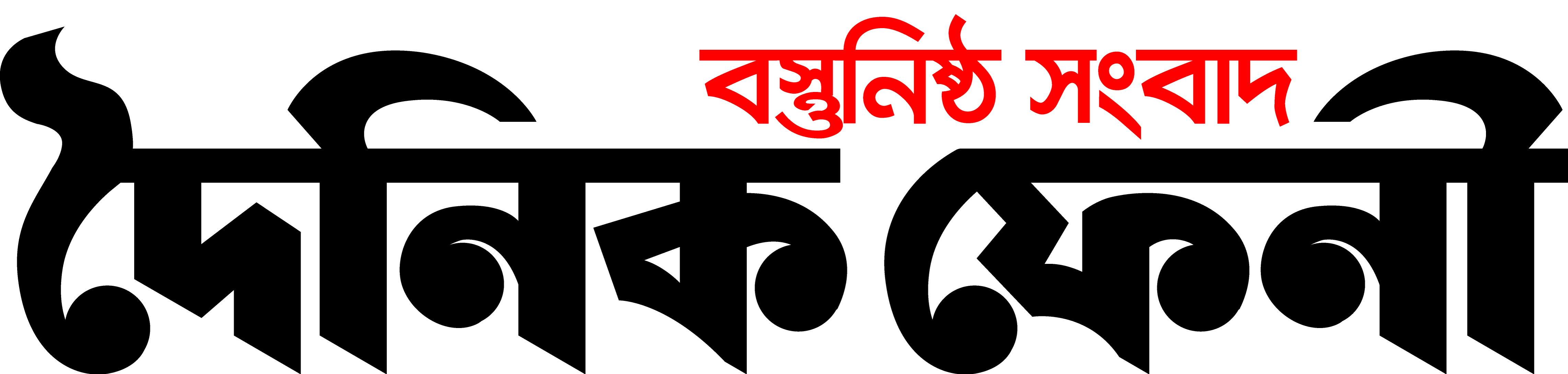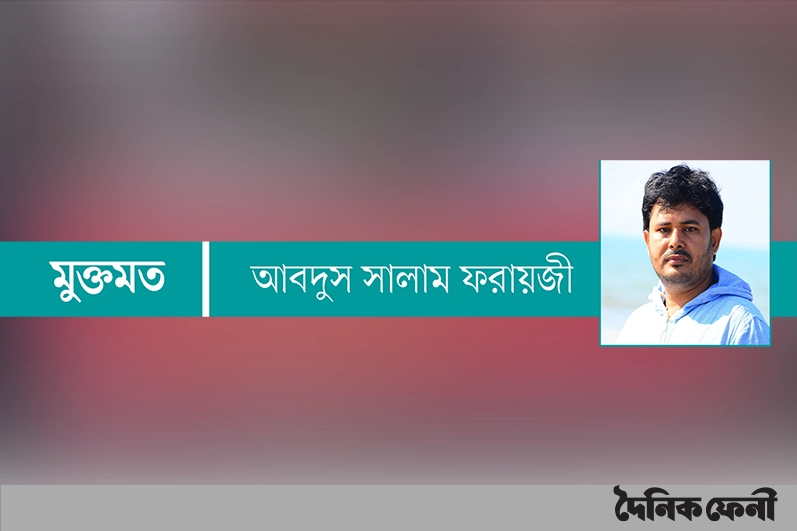বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অদৃশ্য বিপর্যয়। এমন বিপর্যয়, যাকে চোখে দেখা যায় না; তাই ভয়ও নেই। যে বিপর্যয় আমাদের হাসপাতালের বিছানা, বাজারের খাদ্য, পানির নালী, এমনকি শিশুর শরীরের ভেতর দিয়ে নীরবে ছড়িয়ে পড়ছে; অথচ কেউ টের পাচ্ছে না। সময়ের সবচেয়ে ভয়ংকর স্বাস্থ্য সতর্কবার্তাগুলোর একটি—অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকারিতা—বাংলাদেশে আজ আর দূরের হুমকি নয়; বরং আমাদের শরীর, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভেতরেই বাসা বেঁধেছে। আন্তর্জাতিক পত্রিকাগুলোর ভাষায়, এশিয়া—বিশেষ করে বাংলাদেশ—বিশ্বের ‘অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের রাজধানী’ হয়ে উঠছে।
যে অ্যান্টিবায়োটিক মানবসভ্যতাকে মৃত্যু-নিশ্চিত সংক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল, সে অস্ত্রই আজ মানুষের শরীরে ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের শতবর্ষী অগ্রগতি থমকে যাচ্ছে কিছু মানুষের অজ্ঞতা, কিছু মানুষের বাণিজ্যিক লোভ, আর রাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে। যখন একটি জাতি তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধকে অকার্যকর করে ফেলে—তখন সেই জাতির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে শুধু এক অমোঘ ভবিষ্যৎ—ধ্বংস।
এই লেখায় আমরা বাংলাদেশে অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকারিতার নেপথ্যের গভীর কারণ, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, খাদ্যশিল্পের ভেতরে লুকানো মৃত্যু-তথ্য, হাসপাতালব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, এবং নীতি-অবহেলার বহুমাত্রিক সঙ্কট বিশ্লেষণ করব। এবং একইসাথে তুলে ধরব—কীভাবে এই সংকট আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
বাংলাদেশের হাসপাতালের ভিতরে যারা কাজ করেন, তাদের কাছে এই সংকট নতুন নয়। সরকারী হাসপাতালের ওয়ার্ডে যে রোগী সকালে জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়, বিকালে দেখা যায় তার শরীরে দেওয়া অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না। ডাক্তাররা অ্যান্টিবায়োটিক বদলাচ্ছেন, ডোজ বাড়াচ্ছেন, নতুন অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন—কিন্তু ফলাফল শূন্য। জাতীয় পত্রিকার অনুসন্ধান বলছে—সংক্রমণজনিত গুরুতর রোগীদের একটি বড় অংশকে চিকিৎসা দিতে গিয়ে চিকিৎসকরা অ্যান্টিবায়োটিকের ‘শেষ লাইন’-এ চলে যাচ্ছেন; যেগুলো সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে বা দুর্যোগ পরিস্থিতিতে রোগীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
ধীরে ধীরে এই ‘শেষ লাইন’-এর অ্যান্টিবায়োটিকও কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে। দেশে হাসপাতাল-সংক্রমণের যেসব ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যাচ্ছে, তার বড় অংশই বহুধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি প্রতিরোধী। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়—এগুলো ‘সুপারবাগ’। এই সুপারবাগ শুধু চিকিৎসা ব্যয় বাড়াচ্ছে না; বরং ভবিষ্যতে সাধারণ কাটা-ছেঁড়াও প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কবার্তা খুব স্পষ্ট—আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বে বছরে ১ কোটি মানুষ মারা যেতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকারিতার কারণে। আর দক্ষিণ এশিয়াই হবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল।
এই বাস্তবতার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ—যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক শুধু ওষুধ নয়; একটি ‘দৈনন্দিন অভ্যাস’। মাথাব্যথা? অ্যান্টিবায়োটিক। ঠান্ডা? অ্যান্টিবায়োটিক। কাশি? অ্যান্টিবায়োটিক। জ্বর? অ্যান্টিবায়োটিক। এমনকি ভাইরাসজনিত রোগেও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে—যেখানে অ্যান্টিবায়োটিকের ন্যূনতম ভূমিকা নেই। দেশের ওষুধের দোকানগুলো প্রেসক্রিপশন ছাড়াই অ্যান্টিবায়োটিক দিতে অভ্যস্ত। অনেকেই নিজেরাই কিনে খান। কেউ শরীরে সামান্য দুর্বলতা পেলেই ‘শক্তিশালী ওষুধ’ খুঁজতে যান—যার ফলে শরীরের ভেতরে প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয়।
কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকারিতার উৎস শুধু হাসপাতাল নয়—আরও বড় উৎস লুকিয়ে আছে আমাদের খাবারে। জাতীয় পত্রিকাগুলোর অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টগুলো বলছে, দেশের পোলট্রি শিল্পে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পরিমাণ ভয়ংকর। মুরগির বৃদ্ধি দ্রুত করতে, রোগ প্রতিরোধ করতে এবং উৎপাদন বাড়াতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত অ্যান্টিবায়োটিক মেশাচ্ছে খাবারে ও পানিতে। কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত অতি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধেরই সমতুল্য। মুরগির শরীরে সেই ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। এরপর যখন মানুষ এই মাংস খায়—সেই প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।
আবার মাছচাষ খাতে ব্যবহার হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপক প্রয়োগ। পুকুরে রোগ ঠেকাতে, মাছের বৃদ্ধি বাড়াতে অবাধে অ্যান্টিবায়োটিক মেশানো হয়। এভাবে খাদ্যশিল্পের ভেতরে যে প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়, তা মানুষের শরীরে ঢুকে ধীরে ধীরে দখল নিতে শুরু করে। খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের তদন্ত প্রতিবেদন, আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র এবং পত্রিকার তথ্য—সবই দেখাচ্ছে যে বাংলাদেশের খাদ্যশিল্প এখন অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান উৎস।
এখন যদি হাসপাতাল, কৃষি এবং পরিবেশ এই তিনটির চক্রকে একসাথে দেখা যায়—তাহলে স্পষ্ট হয় যে সংকট কতটা বহুমাত্রিক। শহরের ড্রেন, নর্দমা, বর্জ্যপানি এবং অপরিশোধিত নিকাশি পথেও প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে—ঢাকার বর্জ্যপানি ব্যবস্থাপনা অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়ার বড় মাধ্যম।
একজন রোগীর শরীর থেকে নিঃসৃত প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া পানি বা মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে; এরপর সেই পানি নদীতে যায়; নদীর মাছ সেটা বহন করে; তারপর তা বাজারে আসে; সেখান থেকে মানুষের শরীরে। এভাবে প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়ার একটি অদৃশ্য রাষ্ট্র গড়ে উঠছে বাংলাদেশে—যার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা নেই, অস্ত্র নেই, কৌশল নেই।
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাও এই সংকটকে আরও গভীর করেছে। দেশের বেশিরভাগ হাসপাতালে উন্নত রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা নেই। ফলে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা না করেই সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে শুরু করেন। রোগ না সাড়লে ডোজ বাড়ানো হয়, নতুন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। এতে রোগীর দেহে অ্যান্টিবায়োটিকের এক ধরনের ‘অতিব্যবহার’ ঘটে, যার ফল ভয়াবহ। আবার অনেক সময় রোগীরা নিজেরা ওষুধের কোর্স শেষ করেন না; দু–তিন দিন ভালো লাগলেই ওষুধ বন্ধ করে দেন। এতে দেহের ভেতর ব্যাকটেরিয়া পুরোপুরি ধ্বংস হয় না; বরং তারা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে—এবং অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকারিতা বাড়ে।
বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসচেতনতার ঘাটতিও বড় একটি কারণ। দেশের বড় অংশের মানুষ এখনও মনে করেন—‘শক্তিশালী ওষুধই ভালো ওষুধ’। তারা জানেন না যে অযথা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া ভবিষ্যতে নিজের জীবনকেই ঝুঁকিতে ফেলছে। গ্রামের মানুষ প্রথমেই ওষুধের দোকানে যান; শহরের মানুষ নিজেরাই ওষুধ কিনে খেয়ে নেন; অনেকেই চিকিৎসককে না দেখেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করেন।
কিন্তু এই সংকট কেবল চিকিৎসা বা খাদ্য বা পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—এটি একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সংকট। অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকারিতা বৃদ্ধি পেলে হাসপাতালের খরচ বাড়ে, চিকিৎসা দীর্ঘ হয়, কর্মক্ষমতা কমে যায়। দেশের অর্থনীতিতেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে—অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শ্রমঘণ্টার ক্ষতি, চিকিৎসা ব্যয় এবং মৃত্যুহার—সবই বাড়ছে। বাংলাদেশও সেই ঝুঁকির বাইরে নয়।
এখন প্রশ্ন—এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী?
সমাধান রয়েছে তিনটি বড় স্তরে। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় নীতি–কাঠামোকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করতে হবে। ওষুধ প্রশাসনকে কঠোরভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কৃষিখাতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার সীমিত করতে হবে। খাদ্যশিল্পে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ওপর কঠোর নজরদারি চালাতে হবে, প্রয়োজন হলে আইন সংশোধন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, হাসপাতালব্যবস্থাকে আধুনিক করতে হবে। উন্নত রোগ নির্ণয় কেন্দ্র বাড়াতে হবে। চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ জোরদার করতে হবে—যাতে তারা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা অনুসরণ করেন। একইসাথে হাসপাতালে স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। তৃতীয়ত, জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। গণমাধ্যম, সামাজিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—সবাইকে এতে অংশ নিতে হবে। স্কুল–কলেজে স্বাস্থ্যশিক্ষা জরুরি। টেলিভিশন ও সামাজিক মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক সচেতনতা প্রচার করতে হবে।
এখনই সিদ্ধান্ত না নিলে আগামী দুই দশকের মধ্যে বাংলাদেশ এক ভয়ংকর স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। তখন কেবল হাসপাতালই নয়—সমাজের প্রতিটি পরিবার শোকের মুখোমুখি হবে। সাধারণ সংক্রমণ হবে প্রাণঘাতী; সাধারণ অস্ত্রোপচারও হবে ঝুঁকিপূর্ণ; শিশু–বয়স্ক সবাই হবে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে। একসময় যে অ্যান্টিবায়োটিক মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনত, সেই অ্যান্টিবায়োটিকই তখন হবে মূল্যহীন—অকার্যকর।
আজ বাংলাদেশের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেবল একটি প্রশ্ন—আমরা কি এই সংকটকে এখনই গুরুত্ব দেব, নাকি অপেক্ষা করব যতক্ষণ না হাসপাতালের বিছানাগুলো কান্নায় ভরে ওঠে? সিদ্ধান্ত আমাদেরই!
লেখক ও সংগঠক