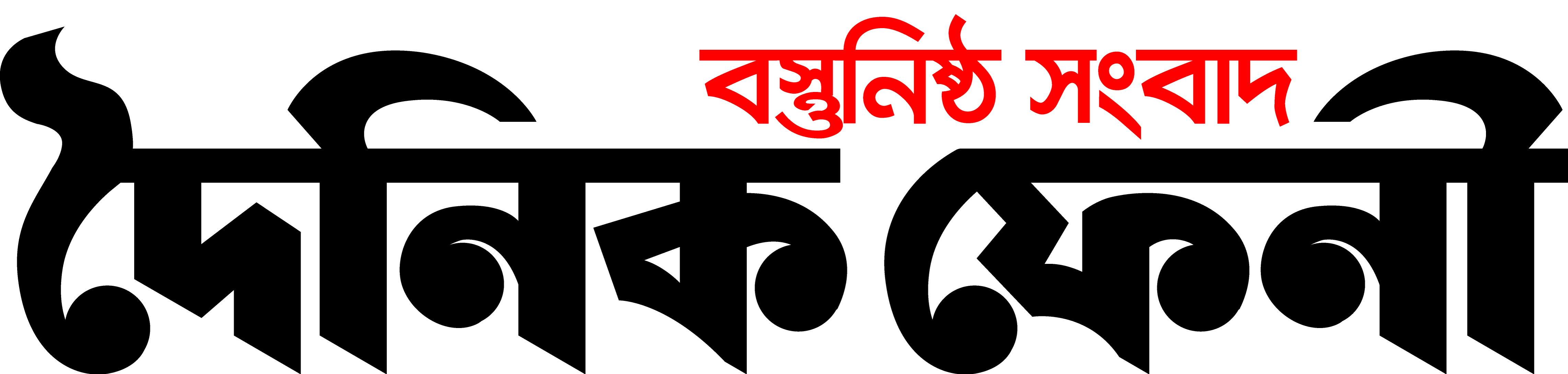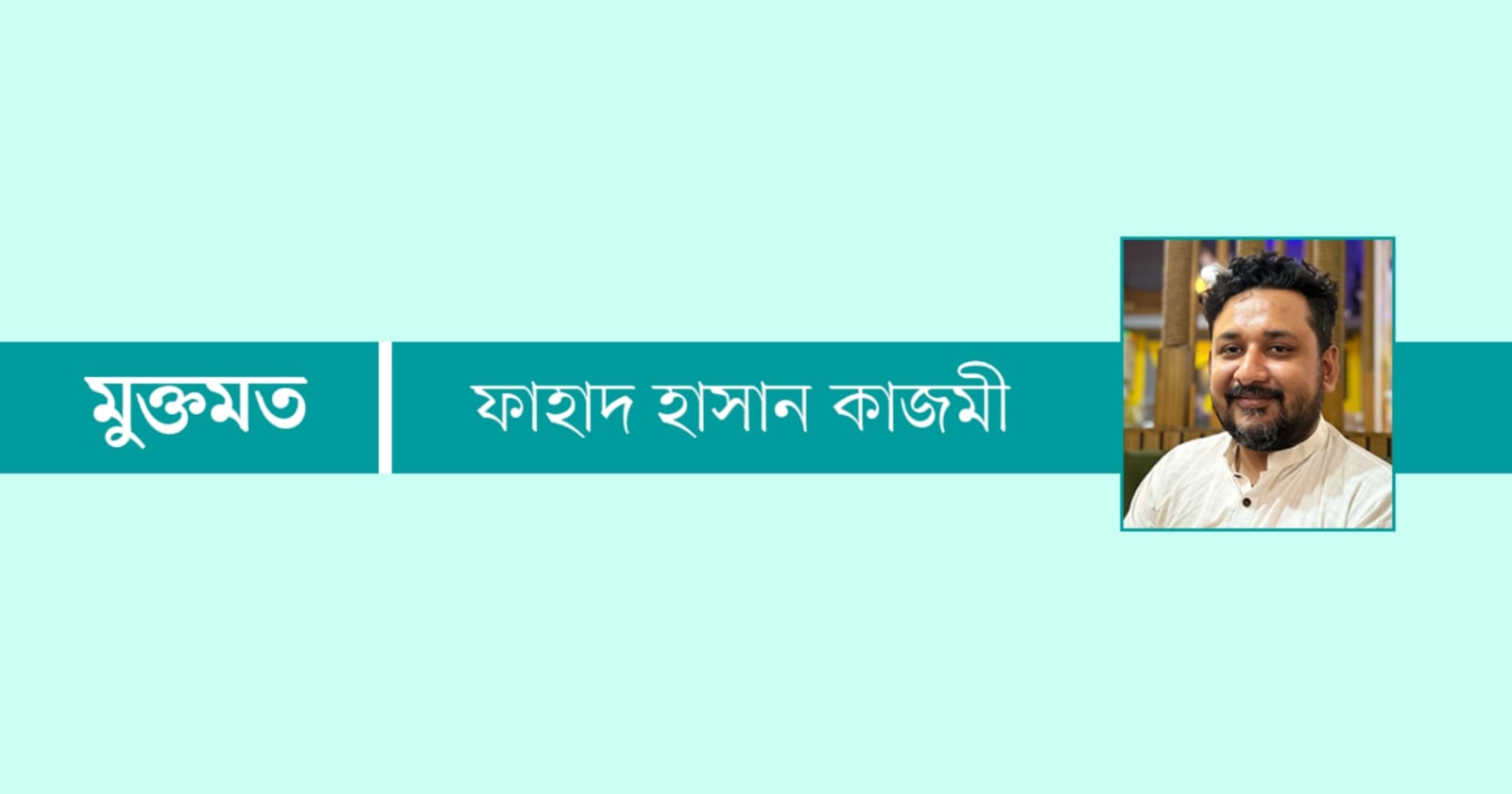বাংলাদেশের ইতিহাসে বাউল, ফকির, বয়াতী-এরা কখনো শুধু গানশিল্পী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন পথের দার্শনিক, মাটির ভাষ্যকার, মানুষের দুঃখ-আকুলতা, প্রেমবিরাগ, ধর্মসমাজ সবকিছু নিয়ে হাজার বছরের কথনশিল্পের ধারক। আর সেই ধারারই এক শিল্পী আবুল সরকার। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর গ্রেপ্তার বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে যে দাগ তৈরি করেছে, তা সামান্য কোনো প্রশাসনিক ঘটনাও নয়; এটি এক বড় ধরনের সংকেত—আমরা কি সত্যিই বুঝতে পারছি না যে লোকসংস্কৃতির ওপর আঘাত মানে দেশের আত্মার ওপর আঘাত?
আবুল সরকার দীর্ঘদিন ধরে মফস্বলপল্লির মানুষের মধ্যে বিচরণ করেছেন লোকগানের ধারায়। তাঁর গান ধর্মীয় গোঁড়ামির বাইরে মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক প্রশ্নকে সামনে আনে—যা বাউল ফকিরিয়া ধারার প্রকৃত স্বর। তাঁর গান কখনো রাজনৈতিক উত্তেজনা নয়; বরং মানুষের ভেতরের জিজ্ঞাসা, সন্ধান এবং মুক্ত আত্মার আহ্বান। অথচ এমন একজন শিল্পীর গান ও মত প্রকাশকে কেন্দ্র করে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা দেখা যায় একক কোনো ফল নয় বরং একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতার অংশ— যেখানে লোকশিল্পী, বাউল, জারি-বাউল বয়াতীরা নানা সময়ে হামলা, মামলা বা চাপের মুখে পড়ছেন।
বাংলার লোকশিল্প একটি বিকল্প যুক্তিধর্ম। এখানে সত্য প্রশ্নে, যুক্তিতে, মানবতায়। বাউলরা ঈশ্বর খোঁজেন শরীরে, মানুষে, দয়ার বিস্তারে— মসজিদ, মন্দিরের সীমানার বাইরে। আর এই দর্শন স্বাভাবিকভাবেই মৌলবাদী রাজনীতিকে অস্থির করে। যে রাজনীতি একক ব্যাখ্যা, একক বিশ্বাস এবং একক আনুগত্য দাবি করে, তার চক্ষুশূল হয়ে ওঠে বাউলের বহুস্বরে বলা মুক্তির গান।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর রচনায় বলেছেন, “বাংলার পল্লীর প্রতিটি পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে।” তিনি আরও বলেন, পাখির কলতান, শিশুর খেলাধুলার ছড়া, পানির শব্দ—এসবই সাহিত্য ও সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার। তাঁর এই ব্যাখ্যায় লোকগানকে কেবল সঙ্গীত নয়, বরং জাতির ভাষিক—সাংস্কৃতিক স্মৃতি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আবার ফোকলোর গবেষক আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর লোকসাহিত্যের কাজে দেখিয়েছেন, গ্রামীণ মানুষের এই গান-কথাই ইতিহাসের বিকল্প দলিল— যেখানে রাষ্ট্রীয় আখ্যানের বাইরে মানুষের বাস্তব জীবন উঠে আসে। ঠিক এই কারণেই লোকগান শুধু বিনোদন নয়; এটি একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা।
এই চেতনার ওপর আঘাত নতুন নয়। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর থেকে দেশের নানা এলাকায় কয়েকজন বাউল ও বয়াতীকে গ্রেফতার, হেনস্তা বা মঞ্চ ভাঙা হয়েছে। কারও বিরুদ্ধে ’ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত’ ধারা, কারও বিরুদ্ধে ‘উসকানি’। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো ছিল স্থানীয় গোষ্ঠীর চাপ, মৌলবাদী রাজনীতির উত্তেজনা এবং অজ্ঞতার মিশ্রণে তৈরি অভিযোগ। আইন ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয়েছে ভয় দেখানোর হাতিয়ার হিসেবে। এর প্রভাব ভয়াবহ—অনেকে এখন আর খোলাখুলি গান গাইতে সাহস পান না, অনুষ্ঠান কমে যাচ্ছে, নতুন প্রজন্ম ভয়ে লোকগান শেখা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।
রাষ্ট্র যদি শিল্পীর সুরক্ষায় না দাঁড়ায়, তবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বেরই মূল্য নেই। কারণ একটি দেশের অস্তিত্ব কেবল তার সরকারি ভবন, আইন প্রণয়ন বা ভৌগোলিক মানচিত্রে নয়; দেশ টিকে থাকে তার ভাষা, লোককথা, গান, স্মৃতি এবং মানুষের হৃদয়ের ভেতরের সংস্কৃতিতে। লোকশিল্প সেই হৃদয়ের সরাসরি ভাষা। এই ভাষাকে দমন করা মানে নিজেকে আঘাত করা। এগুলো তাই শুধু আবুল সরকারের সমস্যা নয়—এটা আমাদের জাতিসত্তার সংকট।
পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায়— যে সমাজ নিজের লোকসংস্কৃতিকে হত্যা করে, সে দীর্ঘদিন টিকে থাকে না। ইউরোপের ফোকলোর সোসাইটি কিংবা আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ফোকলাইফ সেন্টার যুগ যুগ ধরে তাদের লোককাহিনি-লোকগান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ করছে। আর আমরা, যারা বাউল লালন, হাসন রাজা, শাহ আবদুল করিমের উত্তরাধিকারী—আমরা নিজেরাই সেই উত্তরাধিকারকে পুলিশি মানসিকতায় ক্ষতবিক্ষত করছি!
প্রশ্ন হলো—কারা এই দমনযজ্ঞ পরিচালনা করছে? স্পষ্টভাবেই বলা প্রয়োজন— মৌলবাদী রাজনীতি এর প্রধান উৎস। তারা ধর্মের ব্যাখ্যাকে সংকীর্ণ করে সমাজে ভয়ের আবহ তৈরি করে। তাদের মূল কৌশল হলো— ভিন্নমতকে ধর্মীয় অপরাধে রূপান্তর করা, শিল্পকে ‘অবিশ্বাস’ হিসেবে উপস্থাপন করা, এবং জনগণের আবেগকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা। মৌলবাদীর হাতে ক্ষমতা গেলে যে প্রথম আঘাত পড়ে, তা মানুষের স্বাধীন কণ্ঠের ওপর—আর বাউলদের কণ্ঠ তার প্রথম লক্ষ্য। কারণ বাউলদের মুক্তচিন্তা, মানবতাবাদী গান ও আন্তঃধর্মীয় ভাবধারা মৌলবাদীর রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি বিরোধী।
কিন্তু রাষ্ট্র যদি এই মৌলবাদী চাপের কাছে নত হয়, তাহলে ক্ষতি রাষ্ট্রেরই। একটি দেশ তার ভিন্নতার ভেতরেই টিকে থাকে। মানুষ যেমন মানুষের মতো থাকতে চায়, সংস্কৃতিও তেমন তার মুক্ত ধারা নিয়ে চলতে চায়। আমরা আজ যদি বাউলদের নীরব করি, আগামীকাল কবি, তার পরদিন শিল্পী, তারপর সাংবাদিক— এভাবে একে একে সব চিন্তার বাতিগুলো নিভে যাবে। আর যখন বাতি নিভে যায়, তখন অন্ধকার কেবল সাংস্কৃতিক নয়—সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবেও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।
লোকশিল্প কোনো বিলাসিতা নয়; এটি মানুষের মানসিক আশ্রয়। বৃষ্টি এলে, ধানের শিষ মাথা দোলালে, হেমন্তে খেজুরের রস উঠলে, বা কারও ঘরে মৃত্যু এলে—মানুষ যে গান গায়, যে গল্প বলে, যে ছড়া উচ্চারণ করে— এটাই জাতির প্রকৃত সাহিত্য। এই সাহিত্যকে রক্ষা করা মানে মানুষকে রক্ষা করা। শহীদুল্লাহ, আশরাফ সিদ্দিকী, দীনেশচন্দ্র সেন—সবাই সেই কথাই বলেছেন। আজ আমরা সেই কথা ভুলে যাচ্ছি, আর রাষ্ট্রও ভুলে যাচ্ছে তার সাংবিধানিক দায়িত্ব।
আবুল সরকারের গ্রেপ্তার তাই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতীক— যেখানে একটি সমাজ নিজেকে ধ্বংসের দিকে ধীরে ধীরে ঠেলে দিচ্ছে। যেভাবে লালনকে একসময় ‘কুফরি’ বলা হয়েছিল, যেভাবে হাসন রাজাকে সমাজে কটূক্তি শুনতে হয়েছিল— ঠিক সেভাবেই আজকের বাউলরা মৌলবাদী রাজনীতির সহজ শিকার। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না— এই হাসন, এই লালন, এই বাউলরাই আজ বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের পরিচয়ের মূল স্তম্ভ।
আমরা যদি লোকশিল্পের কণ্ঠকে দমন করি, তবে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের ওপরই আঘাত করছি। শিশুদের গল্পশেখা কমে যাবে, তরুণের কল্পনা শক্তি দুর্বল হবে, ভাষা শুকিয়ে যাবে। এই সাংস্কৃতিক শুকিয়ে যাওয়া হলো একধরনের আত্মহত্যা। আমরা কি সত্যিই এমন বাংলাদেশ চাই?
তাই আজ প্রশ্ন খুব সরল—আমরা কি মৌলবাদীদের ভয়ে দেশের হাজার বছরের লোকসংস্কৃতি ছুঁড়ে ফেলব, নাকি আমরা দাঁড়াবো বাউল আবুল সরকারের মতো মানুষের পাশে? একটি দেশকে রক্ষা করতে হলে তার সাংস্কৃতিক শেকড়কে রক্ষা করতেই হবে। বাউলদের কণ্ঠরোধ রোধ করা মানে মানুষের মুক্তচিন্তাকে রক্ষা করা। এটি কোনো ‘এলিট সংস্কৃতি’ নয়— এটা আমাদের মাটির গন্ধ, আমাদের ভাষার জল, আমাদের অস্তিত্বের ভিত।
বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখতে গেলে বাউলদের বাঁচাতে হবে। কারণ তারা গান গায় শুধু গানের জন্য নয়— তারা গান গায় মানুষের জন্য। আর মানুষের গান কখনোই গ্রেপ্তার করা যায় না। আমরা যদি আজ আবুল সরকারের মুক্তি দাবি না করি, তবে আগামী প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। এটাই সত্য।
এটাই সময়ের দাবি।
লেখক: চিত্রশিল্পী