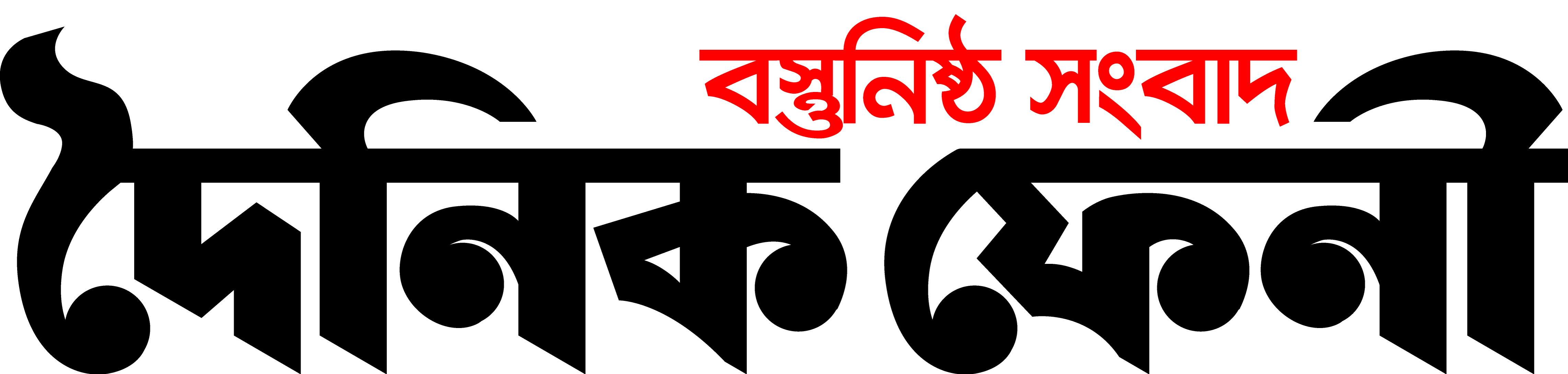ঢাকার ফার্মগেটের দুপুরটা অন্য দিনের মতোই ব্যস্ত ছিল। রাস্তায় অসহ্য যানজট, হর্ণের তীক্ষ্ণ শব্দে ভরা অস্থির নগরজীবন, আর মাথার ওপরে মেট্রোরেলের বিশাল পিলারের সারি। কিন্তু হঠাৎই সেই জীবনের ব্যস্ততার মাঝখানে ধসে পড়ল এক ফোঁটা লোহা— ৮০ কেজি ওজনের বিয়ারিং প্যাড নিচে পড়ে মুহূর্তেই প্রাণ হারালেন শরীয়তপুরের নড়িয়ার আবুল কালাম আজাদ। প্রতিদিনের মতো বের হয়েছিলেন— শুধু সন্তানদের মুখে হাসি ফোটানোর আশায়। কিন্তু যন্ত্রের এক খণ্ড ধাতব ত্রুটিতে মুহূর্তেই থেমে গেল এক জীবনের সব স্বপ্ন।
প্রশ্ন জাগে, এমন মৃত্যু কি কেবলই “দুর্ঘটনা”? নাকি এটি রাষ্ট্রীয় অবহেলার এক নীরব হত্যাকাণ্ড— যার দায় কেউ নেয় না, কিন্তু শিকার হয় বারবার সাধারণ মানুষ? উন্নয়নের নামে নির্মিত প্রতিটি পিলার যদি মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়, তবে সেই উন্নয়নের জয়ধ্বনি কি আদৌ সভ্যতার শোভা বাড়ায়, না বরং লজ্জা বাড়ায়?
আমরা আজ যে উন্নয়নের স্লোগানে মাতোয়ারা— “মেট্রোরেল বাংলাদেশের গর্ব”— সেই গর্বের পেছনে কতটা মানবিক দায়িত্ববোধ কাজ করে? প্রথম আলো ও নিক্কেই এশিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, এর আগেও ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে একই স্থানে একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়েছিল। তখন সৌভাগ্যক্রমে কেউ মারা যাননি। কিন্তু এক বছর পর একই ঘটনায় প্রাণ গেল এক মানুষ। প্রশ্ন উঠেছে— প্রথমবারের দুর্ঘটনার পর কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কোথায় গেল?
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সামছুল হক যথার্থই বলেছেন, “বিয়ারিং প্যাড বসানো হয় সেতু ও পিলারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে; সেটি পড়ে গেলে বুঝতে হবে নকশা ও স্থাপনে গুরুতর ত্রুটি ছিল।” অথচ কর্তৃপক্ষ— ডিএমটিসিএল (Dhaka Mass Transit Company Limited)— এখনো বলছে, “তদন্ত চলছে।” এই দুটি শব্দই যেন আজ রাষ্ট্রীয় দায় এড়ানোর স্থায়ী ঢাল হয়ে গেছে। তদন্ত হয়, রিপোর্ট আসে না; মৃত্যু হয়, কিন্তু বিচার হয় না। প্রশ্ন রয়ে যায়— এই দায়বদ্ধতা কোথায় হারিয়ে গেল?
মেট্রোরেল প্রকল্পের প্রতি কিলোমিটার নির্মাণ ব্যয় ১,৬০০ কোটি টাকারও বেশি— যা ভারত বা মালয়েশিয়ার তুলনায় তিন গুণ। কিন্তু এই বিপুল অর্থ ব্যয় করেও নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো না কেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্থানীয় সাব-কন্ট্রাক্টরদের মাননিয়ন্ত্রণ ছিল দুর্বল, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কোনো প্রটোকল ছিল না। অর্থাৎ সমস্যা শুধু প্রযুক্তিগত নয়, মানসিকতাতেও। উন্নয়ন আমাদের কাছে এখন কেবল গৌরবের প্রতীক, কিন্তু তার নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে পেশাদারিত্ব, দায়িত্ববোধ আর মানবিকতা। অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের ভাষায়, “আমরা পরিসংখ্যানে গর্ব করি, কিন্তু জীবনের মূল্য হারিয়ে ফেলেছি।” তাহলে কি রাষ্ট্র এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে ‘উন্নয়ন’ মানে কেবল ব্যয়, কিন্তু ‘নিরাপত্তা’ মানে বিলাসিতা?
ফার্মগেটের মর্গের সামনে কালামের স্ত্রী বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদের ছোট্ট সন্তান, যার কণ্ঠে প্রশ্ন—“বাবা কখন আসবে?” রাষ্ট্র কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে? সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা এসেছে— কিন্তু একটি শিশুর ভবিষ্যৎ কি টাকার অঙ্কে মাপা যায়? একজন সাধারণ মানুষ যখন রাষ্ট্রীয় অবহেলার কারণে প্রাণ হারায়, তখন সেটি কেবল দুর্ঘটনা নয়— এটি এক প্রশাসনিক হত্যাকাণ্ড। কিন্তু আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রতিবারই “তদন্ত চলছে” বলে খবর শেষ হয়ে যায়। প্রশাসনিক অসাড়তা যেন এখন আমাদের স্বাভাবিক বাস্তবতা। নীতিনির্ধারকেরা যদি কেবল তদন্তে সময় নেন, কিন্তু ব্যবস্থায় না ফেরেন, তবে সেটি কেবল অবকাঠামোর নয়, মানুষের নৈতিক ভিত্তিরও পতন ঘটায়। উন্নয়নের পিলারের মতোই আমাদের সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ ও রাষ্ট্রীয় জবাবদিহি একে একে খুলে পড়ছে।
আন্তর্জাতিকভাবে দেখলে পার্থক্যটি আরও তীব্র। সিঙ্গাপুর, জাপান কিংবা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোতে অবকাঠামো প্রকল্পে একটি দুর্ঘটনাই বড় নিরাপত্তা সংস্কারের সূচনা করে। টোকিও মেট্রো প্রকল্পে ১৯৮৯ সালে একজন কর্মী মারা গেলে পরের সপ্তাহেই ৪৭টি নিরাপত্তা প্রোটোকল নতুন করে প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে একই জায়গায় এক বছর পর একই ধরনের মৃত্যু ঘটে, অথচ নিরাপত্তা নীতিতে কোনো নতুন পদক্ষেপ নেই। বিশ্বব্যাংক ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে সতর্ক করেছিল— “দক্ষিণ এশিয়ার অবকাঠামো প্রকল্পে মানবনিরাপত্তা উপেক্ষিত; এর দীর্ঘমেয়াদি ফল হবে জনগণের আস্থার পতন।” ঠিক সেটিই এখন ঘটছে। উন্নয়ন বাড়ছে, কিন্তু আস্থা কমছে। রাষ্ট্রের প্রকল্প যত বড় হচ্ছে, জনগণের বিশ্বাস তত ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।
অর্থনীতিবিদ ড. নুরুল ইসলাম একবার বলেছিলেন, “রাষ্ট্রের শক্তি মাপা হয় তার পিলার কত উঁচু তা দিয়ে নয়, বরং তার নাগরিক কত নিরাপদ তা দিয়ে।” আমরা হয়তো প্রযুক্তিগতভাবে এগোচ্ছি, কিন্তু মানবিকভাবে পিছিয়ে যাচ্ছি। আমাদের রাস্তাঘাটে, নির্মাণস্থলে, শিল্পকারখানায় প্রতিদিন যে মৃত্যুর মিছিল চলছে, তা আর ‘দুর্ঘটনা’ বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) জানিয়েছে, ২০২৪ সালে শুধু নির্মাণ খাতে ৩৮০ জন শ্রমিক মারা গেছেন— যার মধ্যে ৭০ শতাংশের কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এই পরিসংখ্যান আমাদের বিবেকের আয়না হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা সেটিকে সংবাদপত্রের একটি দিনের খবর হিসেবে ভুলে যাই।
আবুল কালামের মৃত্যু তাই কেবল একটি পরিবারের ট্র্যাজেডি নয়; এটি রাষ্ট্রীয় নীতির ব্যর্থতার প্রতীক। রাষ্ট্র যখন নাগরিকের জীবন রক্ষা করতে পারে না, তখন তার উন্নয়ন যত বড়ই হোক, সেটি শূন্যতার ওপর দাঁড়ানো এক কাচের প্রাসাদ। সেই প্রাসাদ দেখতে চকচকে, কিন্তু ভিতরটা ফাঁপা। আমরা আজ যে দেশে বাস করছি, সেখানে উন্নয়ন দৃশ্যমান, কিন্তু মানুষ অদৃশ্য; পিলার উঁচু হচ্ছে, কিন্তু নৈতিকতা নিচে নেমে যাচ্ছে।
তাহলে আমরা কোন পথে যাচ্ছি? উন্নয়নের মহাসড়কে, নাকি সহমর্মিতার গহ্বরে? উন্নয়ন তখনই উন্নয়ন, যখন তা মানুষের জীবনকে রক্ষা করে, মৃত্যু নয়। যদি একটি রাষ্ট্র তার নাগরিকের প্রাণকে রক্ষা করতে না পারে, তবে সেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন আসলে মৃত্যুর ওপর দাঁড়ানো এক বালুর বাঁধ। আবুল কালাম আজাদ যেন ভুলে যাওয়া আরেকটি নাম না হন। তাঁর মৃত্যু আমাদের সামনে এক আয়না ধরেছে— যেখানে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রযুক্তিগত নয়, মানবিক বিপর্যয়।
এখন সময় এসেছে স্লোগান নয়, প্রশ্ন করার। প্রকল্প নয়, জবাবদিহির। রাষ্ট্র যদি সত্যিকার উন্নত হতে চায়, তবে তাকে প্রথমে মানবিক হতে হবে। কারণ, একদিন সেই পিলারগুলো যদি ভেঙে পড়ে, তারা শুধু লোহা নয়— তারা ভেঙে দেবে রাষ্ট্রের বিবেকও। আর তখন উন্নয়ন নয়, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।
লেখক ও সংগঠক