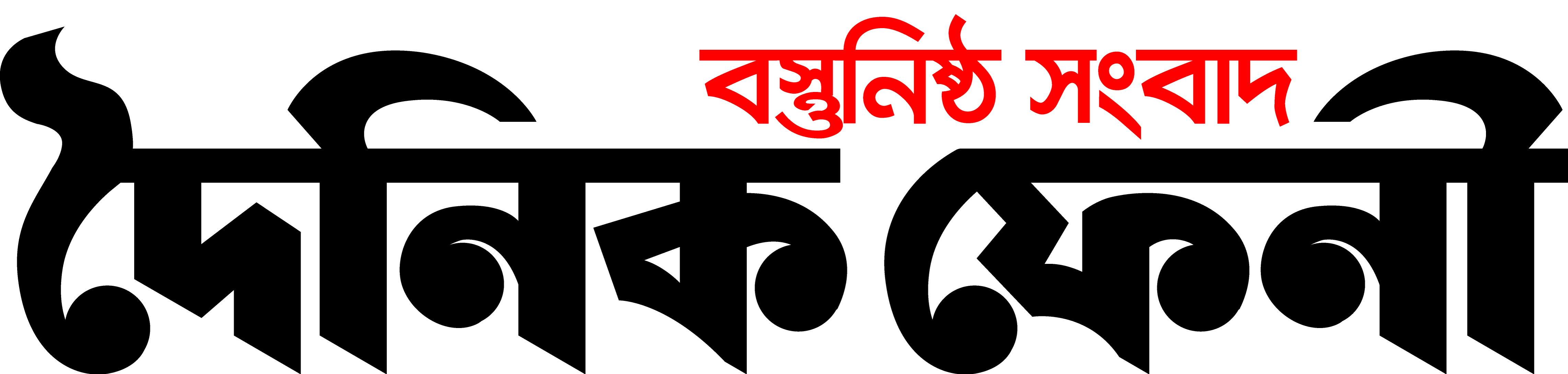বাংলাদেশে ২২ অক্টোবর—জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা দিবস। প্রতি বছর এই দিনে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একই স্লোগান উচ্চারিত হয়—“নিরাপদ সড়ক সবার অধিকার।” কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই স্লোগানের প্রতিধ্বনি রাস্তায় কতটা বাস্তবতা পেয়েছে? দুর্ঘটনার সংখ্যা কি কমেছে, নাকি বেড়েছে? ২০২৫ সালের প্রথম নয় মাসে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদন বলছে— তিন হাজার পাঁচশ’টিরও বেশি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন চার হাজারেরও বেশি মানুষ। অর্থাৎ প্রতিদিন কমপক্ষে চৌদ্দটি প্রাণ হারাচ্ছে রাস্তায়। এটি কোনো সংখ্যা নয়, এটি একেকটি পরিবার, একেকটি অসমাপ্ত গল্পের সমাপ্তি। অথচ রাষ্ট্র যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছে এই মৃত্যুর সাথে— যেন আরেকটি দিন, আরেকটি ফুল, আরেকটি আনুষ্ঠানিকতা। প্রশ্ন জাগে—যে দেশে প্রতিদিন মৃত্যু ঘটে সড়কে, সেখানে “নিরাপত্তা দিবস” উদযাপন মানে কী? এই দিবস কি আত্মসমালোচনার, নাকি আত্মতুষ্টির? নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি যদি কেবল বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে এটি হয়ে ওঠে কেবল এক প্রশাসনিক উৎসব— যেখানে জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয় ব্যানার আর করতালি। সরকার বলছে— সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে কঠোর আইন ও নজরদারি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাস্তবে দেখা যায় উল্টো চিত্র। লাইসেন্সবিহীন চালক, ফিটনেসবিহীন যান, অতিরিক্ত বোঝাই ট্রাক, বেপরোয়া গতি— সবই প্রতিদিনের বাস্তবতা। ট্রাফিক সিগন্যালের প্রতি অনীহা, ওভারটেকিং প্রতিযোগিতা, কিংবা পথচারীর প্রতি সহানুভূতির অভাব— এইসব মিলেই সড়ক যেন হয়ে উঠেছে এক যুদ্ধক্ষেত্র।
২০১৮ সালে প্রণীত “সড়ক পরিবহন আইন”কে বলা হয়েছিল যুগান্তকারী। কিন্তু বাস্তবে তার প্রয়োগ যেন এক অলিখিত রসিকতা। রাজনৈতিক চাপ এলে আইন শিথিল হয়, চালক সংগঠন আন্দোলনের হুমকি দিলে সরকার পিছু হটে। প্রশ্ন ওঠে—যখন আইন শক্তির মুখে নমনীয় হয়ে যায়, তখন আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ টিকবে কীভাবে? বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় ৪০ লাখ চালকের লাইসেন্স আছে, কিন্তু সক্রিয়ভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন ৬০ লাখেরও বেশি। অর্থাৎ কমপক্ষে ২০ লাখ চালক এখনো লাইসেন্সবিহীনভাবে রাস্তায়। তাহলে দায় কার? চালকের, না তদারকির? প্রতিটি দুর্ঘটনার পর পুলিশের প্রতিবেদন হয় একইরকম: “চালকের গাফিলতি।” কিন্তু কখনো কি দেখা গেছে পরিবহন মালিক বা রুট পারমিট প্রদানকারীদের জবাবদিহি? ২০১৮ সালের শিক্ষার্থী আন্দোলনের সময় যেভাবে দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যু পুরো দেশকে নাড়া দিয়েছিল, তা কি সত্যিই কোনো স্থায়ী পরিবর্তন এনেছিল? বরং বছর না ঘুরতেই দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে গেছে।
আমরা বারবার নিচুস্তরের চালককে দোষী বলি, কিন্তু মূল কাঠামোতে যারা দায়িত্বে, তাদের দায় কোথায়? একজন চালক যখন সময়ের চাপে গাড়ি চালায়, যখন তাকে বলে দেওয়া হয়—“আজ তিন ট্রিপ না দিলে চাকরি থাকবে না”—তখন সে নিয়ম মানবে কীভাবে? মূল সমস্যাটা অর্থনৈতিক কাঠামোয়, যেখানে মানুষের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয় মুনাফাকে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন মুখস্থনির্ভর, তেমনি সড়ক ব্যবস্থাও অনুশাসনবিহীন। সবাই দৌড়াচ্ছে, কেউ থামে না। “আমি আগে যাব”—এই মানসিকতা এখন জাতীয় রোগে পরিণত হয়েছে। ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করা যেন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো যেন আধুনিকতার প্রতীক। সমাজ যখন নিয়মভঙ্গকে স্বাভাবিক করে ফেলে, তখন সড়কে মৃত্যু আর বিস্ময় জাগায় না—সেটি হয়ে যায় দৈনন্দিন সংবাদ।
রাষ্ট্র যখন “স্মার্ট বাংলাদেশ” গড়ার কথা বলে, তখন প্রশ্ন জাগে—এই স্মার্ট প্রযুক্তির দেশে কেন রাস্তায় প্রতিদিন প্রাণ হারায় সাধারণ মানুষ? ঢাকায় এখন প্রায় দশ লাখ মোটরসাইকেল চলাচল করছে, যার ৪০ শতাংশই নিবন্ধনবিহীন। বছরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহতদের ৬০ শতাংশের বয়স আঠারো থেকে ত্রিশ। অর্থাৎ যারা দেশ গড়ার বয়সে, তারাই মৃত্যুর পরিসংখ্যানে পরিণত হচ্ছে।
সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ করছে, কিন্তু নিচে ট্রাফিক দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যাল লাগানো হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো কাজ করছে না। “স্মার্ট বাংলাদেশ” গড়তে হলে আগে দরকার “সচেতন বাংলাদেশ”— যেখানে নিয়ম মানা হবে ভয়ে নয়, দায়িত্ববোধ থেকে। রাজনীতিও সড়কের বড় রোগ। রাস্তায় অবরোধ, মিছিল, সমাবেশ— সবই রাজনীতির হাতিয়ার। কিন্তু এই রাজনীতি যখন প্রশাসনের অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান পায়, তখন সাধারণ মানুষের চলাচল আর নিরাপত্তা পেছনে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর তদন্ত কমিটি হয়, কিন্তু প্রতিবেদন প্রকাশ হয় না। কারণ সেই প্রতিবেদন অনেক সময় পৌঁছে যায় প্রভাবশালী মহলের দরজায়—যেখানে থেমে যায় রাষ্ট্রের কলম।
গণপরিবহন খাতের দিকে তাকালেই বোঝা যায়— এখানে কোনো শৃঙ্খলা নেই। ঢাকার রাস্তায় বাসে উঠলে আপনি জানেন না, সেটি কোন রুটে যাবে, কখন থামবে, কোথায় থামবে। সময়সূচি মানার সংস্কৃতি নেই। দুর্ঘটনা ঘটলে মালিক সংগঠনগুলো পরদিন ধর্মঘট ডাকে—যেন দায় অন্যের। অথচ বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট বলছে, দেশের ৭৪ শতাংশ দুর্ঘটনা প্রতিরোধযোগ্য ছিল যদি চালকের প্রশিক্ষণ, যানবাহনের ফিটনেস ও রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক থাকত। তাহলে কি রাষ্ট্র এই অরাজকতা টিকিয়ে রাখছে ইচ্ছাকৃতভাবে? বিশৃঙ্খলা থেকে তো জন্ম নেয় প্রভাব, ক্ষমতা ও ঘুষের ব্যবসা। সড়ক যেন এখন কেবল রাস্তাই নয়— এটি হয়ে উঠেছে ক্ষমতার প্রতিচ্ছবি।
প্রতিটি দুর্ঘটনার পর শোনা যায়—“জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।” কিন্তু আসলে মানুষ কি সচেতনতার অভাবে মরে, না অব্যবস্থার অভাবে মরে? একজন পথচারী যখন ফুটপাত না পেয়ে রাস্তায় হাঁটে, সে কি আইন ভাঙছে, নাকি রাষ্ট্র তাকে আইন ভাঙতে বাধ্য করছে? একজন চালক যখন ষোলো ঘণ্টা টানা গাড়ি চালায়, সে কি অপরাধী, না পুঁজির দাস?
দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান বা মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলো দেখিয়েছে—সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, যখন একসাথে আইন ও নৈতিকতার সমন্বয় ঘটে। এসব সভ্য দেশের চালকরা জানে, দুর্ঘটনা ঘটলে শুধু শাস্তি নয়, সামাজিক কলঙ্কও আসবে। বাংলাদেশে কি এমন সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে? প্রশাসনের মধ্যে যারা সড়ক পরিচালনার দায়িত্বে, তাদেরও কি নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস আছে? শহরের রাস্তায় যখন পুলিশ নিজের মোটরসাইকেলে হেলমেট ছাড়াই চলাচল করে, তখন নাগরিক কাকে অনুসরণ করবে? ২০২৫ সালের সড়ক নিরাপত্তা দিবসের সরকারি স্লোগান— “জীবনের আগে গতি নয়, নিরাপত্তাই অগ্রগতি।” কিন্তু এই স্লোগানই তো আমরা শুনছি গত দশ বছর ধরে। প্রশ্ন হলো— এই কথাগুলো কেবল ভাষণমঞ্চে সীমাবদ্ধ থাকলে কী হবে? কবে সেগুলো নামবে রাস্তায়? দিবস পালনের সংস্কৃতি এখন একধরনের কৃত্রিম আত্মপ্রসাদে রূপ নিয়েছে। ফুল দেওয়া, ফিতা কাটা, ব্যানার লাগানো, নেতাদের মাইক্রোফোনে বক্তৃতা দেয়া, হাসি দিয়ে ছবি তোলা আবার সেগুলো ফেসবুকে পোস্ট দেয়া— নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে এগুলো দিয়ে মৃত্যুর পরিসংখ্যান বদলায় না। বরং আমাদের দরকার সঠিক বাস্তবায়ন, কঠোর আইনপ্রয়োগ, সড়ক সংস্কৃতি বদলের প্রচেষ্টা।
রাস্তায় কেউ মারা গেলে আমরা মুহূর্তের জন্য শোক প্রকাশ করি, কিন্তু পরদিনই আবার রুটিন জীবনে ফিরে যাই। যেন মৃত্যু এখন অভ্যস্ত শব্দ। সংবাদপত্রের ছোট কলামে হারিয়ে যায় একেকটি জীবনের গল্প, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কয়েক ঘণ্টার আবেগের পর সবকিছু আবার নীরব হয়ে যায়। সবচেয়ে ভয়াবহ হলো— যখন সমাজ মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়, তখন আর কোনো সংস্কার আন্দোলন টেকে না। সড়ক নিরাপত্তা দিবস তাই এক অর্থে রাষ্ট্রের আত্মসমালোচনার দিন, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটি হয়ে গেছে আত্মতুষ্টির দিন। আমরা কি কখনও এমন এক সকাল কল্পনা করতে পারি, যখন দেশের কোনো সড়কে কেউ মারা যাবে না? হয়তো সে দিনই হবে সত্যিকারের সড়ক নিরাপত্তা দিবস— যেদিন ফুল নয়, ব্যানার নয়, বরং জীবিত মানুষের হাসি হবে উদযাপনের প্রতীক।
নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন তাঁর ব্যক্তিগত শোক থেকে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন ১৯৯৩ সালের ২২ অক্টোবর, সেটি আজ তিন দশক পার করেছে। তিনি চেয়েছিলেন যেন কোনো পরিবার তাঁর মতো আর প্রিয়জন হারায় না। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন কি পূরণ হয়েছে? এখনো প্রতিদিন রাস্তায় মরে যাচ্ছে অসংখ্য জাহানারা কাঞ্চন। একটি হেলমেট, একটি সিগন্যাল মানা, একটি সচেতন সিদ্ধান্ত— হয়তো বাঁচাতে পারে একটি জীবন। কিন্তু আমরা কি প্রস্তুত এতটুকু দায়িত্ব নিতে? রাস্তায় মৃত্যু এখন আর কেবল দুর্ঘটনা নয়— এটি রাষ্ট্রের ব্যর্থতার প্রতীক। সড়ক নিরাপত্তা দিবস তাই শুধু স্মরণ নয়, এটি হওয়া উচিত জাতীয় আত্মসমালোচনার দিন। রাষ্ট্র যদি চায়, আইনের প্রয়োগ, প্রযুক্তি ও শিক্ষার সমন্বয়ে এটি সম্ভব। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক শুদ্ধতা এবং নাগরিক নৈতিকতা।
অবশেষে একটাই প্রশ্ন রয়ে যায়— নিরাপদ সড়কের দাবিতে প্রতি বছর যত ফুল অপচয় হচ্ছে, তত প্রাণ কি আমরা বাঁচাতে পেরেছি ? যদি না বাঁচাতে পারি, তবে এই দিবস কেবলই এক প্রতীকী শোকানুষ্ঠান— রাস্তায় রক্ত ঝরার আগের বা পরের একদিনের আনুষ্ঠানিক অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যিকারের “জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা দিবস” হবে সেই দিন, যেদিন আমরা শুনব—আজ দেশের কোনো সড়কে কেউ মারা যায়নি। সেদিনই হবে জীবনের জয়গান, সভ্যতার গর্ব, আর রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ জবাবদিহির দিন। ততদিন পর্যন্ত এই দিবস যেন আমাদের বিবেককে প্রশ্ন করেই যাবে— “রাস্তায় মৃত্যু, রাষ্ট্র কেন নীরব?”
-লেখক ও সংগঠক